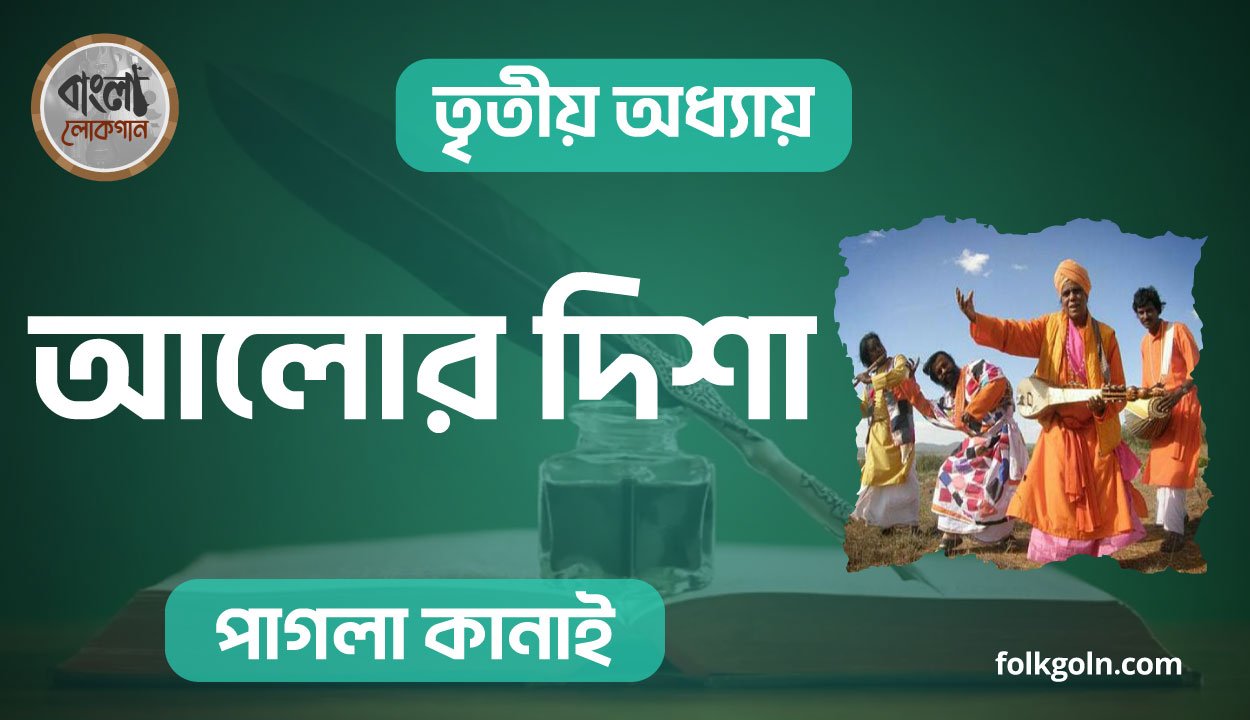আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আলোর দিশা। কুড়োন শেখ আলাদা করে সংসার পাতলেন। ছোট্ট সংসারটিকে তিনি মনের মতো করে সাজাতে গোছাতে চাইলেন। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল । তিনি হঠাৎ করে কানাই-উজোল কে রেখে পরপারে যাত্রা করলেন। নাবালক পুত্রদ্বয়কে নিয়ে মাতা মুমেনা খাতুন ভয়ানক মুছিবতে পড়লেন। তিনি অত্যন্ত দীন-হীনভাবে সংসার ধর্ম পালন করতে লাগলেন। উপায়ন্ত না দেখে জামাই কামালউদ্দিন বিশ্বাস তাঁদের সবাইকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিলেন।

Table of Contents
আলোর দিশা
পূর্বে আমরা আদম লস্করের নাম উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান অথচ সম্পদশালী লোক। ভায়রা-পো দুটিকে তিনি নিজের কাছে নিয়ে যাবার মনস্থ করলেন। শ্যালিকা ও তৎ জামাইকে বলে বালকদ্বয়কে নিজ গৃহে স্থান দিলেন । তিনি তাদেরকে শিক্ষারও বন্দোবস্ত করতে চাইলেন। কিন্তু তাও তাদের ধাতে সইলো না । প্রকৃতির পাগল কি প্রকৃতি ছেড়ে থাকতে পারেন। পাঠশালা ছেড়ে তারা গেলেন কলির কৃষ্ণ হয়ে ধেনু চরাতে।
কালীদহের ধারে ধারে গরু-বাছুর চরানো ও গুন গুন করে গান করে বেড়ানো, এই হল কানাই আর উজলের শিক্ষা ও শিক্ষা কেন্দ্ৰ। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলতে চাই যে চারণ কবি পাগলা কানাই এর পীর-মুর্শিদ- উস্তাদ-গুরু (যাই বলি না কেন) বলে কেউ ছিলেন না। প্রকৃতিই তার শিক্ষাদাত্রী। তিনি ও উজোল খালু আদম লস্করের বাড়ি ভাটপাড়া থাকতেন । ভাটপাড়া নলডাঙ্গা থেকে মাত্র আধামাইল দূরে। এই নলডাঙ্গার জমিদার বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টায় বলতে হয় গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ চলতো।
সেকালের জমিদার, জ্ঞাতিদার, জোতদার, মহাজনেরা সারা রাত গান-বাজনা বা অনুরূপ কোন আমোদ-প্রমোদে ভরিয়ে রাখতো। তৎকালে দস্যু-তস্করের উপদ্রব ঠেকানোর জন্য বাড়িতে লোকজনের সমাগম করে রাখতো। নলডাঙ্গার রাজবাড়িতেও এমনি ধরনের উৎসব লেগেই থাকতো। সেই গান-বাজনা শোনা বা শুনতে যাওয়া কানাই উজলের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।
সে গান-বাজনাতে কানাই-উজোল যে মোহিত হন নি তা কে জানে। এখান থেকেও তারা অনুপ্রাণিত হয়ে গান শিক্ষা করতে পারেন। ‘দেখাদেখি চাষ, দেখাদেখি বাস বলে একটা প্রবাদ আছে। কানাই-উজোল যে একেবারেই গান শোনেননি বা কোথাও যাননি তা বলা যায় না। সময় সুযোগ তাদের কম থাকায় কোন ওস্তাদ ধরতে পারেন নি । ওস্তাদের ভার প্রকৃতিই নিয়েছে। তাদের ধীশক্তির কাছে কোন ওস্তাদের প্রয়োজন হয় নি। এমনি ধরনের অনেক জ্ঞানী-গুণি, ফকির-দরবেশ পাওয়া যায়।
দু’ভাই খালা-খালুর বাড়ি বড়ই আরাম-আয়েশে দিন কাটাতেন বটে, কিন্তু মনে তাদের একটুও শান্তি ছিল না। কী এক অজানা চিন্তায় কবি বিভোর হয়ে থাকতেন । এমনিতেই তিনি ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। সেই ভাবুক প্রকৃতি যেন তাকে আরও ভাবিয়ে তুললো। খালা-খালুর অপত্য স্নেহ তাকে শান্তি দিতে পারলো না। পিতা-মাতার স্নেহ, ভাই-বোনের আদর, জন্মভূমির মায়া, সংগী- সাথীদের ভালবাসা তাকে অস্থির করে তোলেনি বরং সংসারের মায়া-মমতা, কঠিন বাস্তবতা এবং দুর্নীতি পরায়ণ সমাজ ব্যবস্থা তাকে ক্রমশঃ পীড়িত করে তুলতে থাকে ।
ভাটপাড়ার নিকটে ‘কালিকা দহ’ নামে একটা দহ আছে। যার বর্তমান জলাকার ৯ একর । পূর্বে এই জলাশয় আরও বিস্তীর্ণ ছিল। তাছাড়া বর্ষাকালে দহটি তার চতুর্দিকে বিশাল এলাকা প্লাবিত করতো। প্রচণ্ড স্রোতও চলতো এখানে । দহটির একপাশে শ্মশান হিসেবে ব্যাবহার করা হতো। স্বাভাবিকভাবেই শ্মশানের চারি পার্শ্ব বন-জংগলে পূর্ণ ছিল। দহটি মারাত্মক দূষণীয় স্থান বলে পরিচিত ছিল । অর্থাৎ ভূত-প্রেতের আড্ডাখানা ছিল । চৈত্র মাসেও এখানে ৭/৮ হাত পানি থাকে বলে জানা যায়।
কালিদহের মধ্যভাগে দ্বীপাকারে একটুখানি ঢিবি ছিল। সেই দ্বীপ সদৃশ স্থানে একটি বট গাছও ছিল। এর নিচে মাঝে মাঝে কোথা থেকে এক দরবেশ এসে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন । কানাই-উজোল অন্যান্য রাখাল বালকদের সংগে গরু-বাছুর চরাতে যেতেন এবং সেগুলি মাঠে ছেড়ে দিয়ে দরবেশ সাহেবের কার্যকলাপ দেখতেন আর গুন গুন করে গান গাইতেন। বর্তমানে সে দ্বীপ আর বটগাছের কোন আলামত নেই । দহটিও নাজুক অবস্থায় কালের সাক্ষি হয়ে আছে ।
এমনি করেই কানাই উজলের দিন কাটতে থাকে। একদিন দুপুর বেলা গরু চলানোর সময় হঠাৎ করে কবির পেটে ভীষণ ব্যাথা হয় । ইতোপূর্বে এ ধরনের ব্যাথা কখনও দেখা যায় নি। ব্যাথার তীব্রতায় কাটা কবুতরের মতো ছটফট করতে থাকেন। ছোট উজলের সাথে অন্যান্য রাখাল বালক যারা ছিল, কানাইয়ের এই ভয়ানক অবস্থায় হতবাক হয়ে রইল।
এমনই সময় কানাই যেন কার কন্ঠস্বর শুনতে পেলেন। কর্ণে সে স্বর পৌঁছা মাত্র তিনি ক্ষণিকের জন্য স্থীর হয়ে পড়লেন । তাকিয়ে দেখেন, সেই দরবেশ সাহেব তাকে হাতের ঈশারাই ডাকছেন। দরবেশ সাহেব পুনরায় স্নেহ মাখা কণ্ঠে ডাকদিয়ে বললেন, “ওরে পাগলা কাঁদছিস ক্যান? এই পোড়া কাঠখানা ধরে চলে আয়” । এই বলে একখানা কাঠ ভাসিয়ে দিলেন।
বালক কানাই আর স্থির থাকতে পারলেন না। সে ডাক উপেক্ষা করার মতো ক্ষমতাও তার রইল না। তিনি আস্তে আস্তে উঠে দহের ধারে গেলেন। আল্লাহর নাম স্মরণ করে সেই পোড়া কাঠখানি বুকে নিয়ে দরবেশ সাহেবের কাছে গেলেন। বলাবাহুল্য এতক্ষণ তার সেই তীব্র পেটের ব্যাথা কোথায় যেন উবে গেছে। তিনি ভক্তির সাথে দরবেশ সাহেবকে সালাম করলেন। তিনিও তাকে বুকে টেনে নিলেন ।
স্বস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললেন, “পাগল তোর দুঃখ কি? কাঁদছিস ক্যান?”” বালক কানাই ভক্তিভরে আপ্লুত হয়ে পড়লেন। আনন্দস্রোতে চোখ দুটি ভরে গেল । তিনি ভুলেই গেলেন তার ব্যাথার কথা। একে একে বর্ণনা করে গেলেন তার গত জীবনের কথা। সব শুনে ফকির সাহেব কিছু পড়ে কানাইয়ের গায়ে ফুঁক দিয়ে বললেন, “পাগল, এই নামটা শিখে নে। হর-হামেশা জপ করবি। তোর সব মনষ্কামনা পূর্ণ হবে” ।
পরবর্তী কালে ঐ দরবেশ সাহেবের কথা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হতে দেখা যায় । বালক কানাই দরবেশ সাহেবের দেয়া নাম শিখে আবার সেই পোড়া কাঠখানার সাহায্যে এপারে চলে আসলেন। এমন সময় উজোল কর্তৃক খবর পেয়ে খালু আদম লস্করও ছুটে আসলেন। দরবেশ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “আদম, পাগলকে ঘরে নিয়ে যা। ও যা চায়, তা করতে দিস”* । কানাই খালুর সাথে বাড়ি এলেন । সেই থেকে কানাই নামের সাথে পাগল বা পাগলা শব্দটা যুক্ত হয়ে গেল |
বাড়ি এলে পাগলা কানাইয়ের মন হলো চিন্তায় বিভোর । কি করে এমন হলো? মনে তার অনেক শান্তি, অনেক সুখ। হঠাৎ, তার মনে হল দরবেশ সাহেবের কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি। পরদিন প্রভাতে আবার কালিকা দহের আস্তানায় ছুটলেন । কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। বহু অনুসন্ধানের পর ‘সোয়াইব নগর’-এর গভীর জংগলে তাঁকে পাওয়া গেল ।
‘তিনি উর্দ্ধপদে এক গাছের ডালে ঝুলছেন । কানাই কাছে যেতেই দরবেশ সাহেব বলে উঠলেন, কিরে পাগলা? আবার কি কাজে এলি? যা’ পাবার তা’ পেয়েছিস। ফিরে যা। এখানে আর আসিসনে । পাগলা কানাই চিন্তায় বিভোর হয়ে বাড়ির পথ ধরলেন । এই ঘটানার পর দরবেশ সাহেবকে এতদঞ্চলে আর দেখা যায় নি ।

মাতৃ ক্রোড়ে সাধনা
দরবেশ সাহেবের কাছ থেকে ফিরে এসে পাগলা কানাই খালু আদম লস্করকে সব ঘটনা খুলে বললেন। খালু কিছুই বললেন না। তবে, স্নেহের মাত্রা বেড়ে গেল । নিঃসন্তান খালু তার বিষয়-সম্পত্তি কানাই-উজালের নামে দান করতে মনস্থ করলেন কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। পরপারের ডাকে তিনি দেহ রাখলেন। ফলে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি শরীকদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। পথের কাঙ্গাল আবার পথের কাঙ্গাল হলেন ।
খালুর মৃত্যুর পর কানাই-উজোল পুনরায় মাতৃভূমি বেড়বাড়িতে মা ও বোনের কাছে ফিরে এলেন । এ সময় পাগলা কানাই-এর বয়স মাত্র ১৫/১৬ বছর। ক্ষুধা রূপ অনলের দাহ নিবৃতিতে সাড়া না দিয়ে কোন জীবেরই গত্যান্তর নেই । দু’ভাই কাজের সন্ধানে ফিরতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত, “কবি মাত্র ২ টাকা বেতনে আঠারো খাদার বেড়বাড়িস্থ নীলকুঠিতে গোমস্তাগিরির কাজ নিলেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস।
যে নীলকরের অত্যাচারে যারা একদিন সবকিছু হারিয়ে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করেছিলেন, আজ তাঁরা তাদেরই অধীনে সামান্য ২ টাকা বেতনে গোমস্তাগিরির মতো চাকরী করতে বাধ্য হলেন । আমরা পূর্বেই বলেছি, গণ্ডির বাঁধনে থাকা ছিল কবির স্বভাব বিরুদ্ধ। যার ফলে, তিনি লেখাপড়া শিখতে পারেন নি । ৬ মাস যেতে না যেতেই তিনি চাকরী ছেড়ে দিলেন।
ড. মযহারুল ইসলাম সাহেবের কবি পাগলা কানাই’ গ্রন্থে উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে । এ বিষয়ে আমরা অনেক অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি যে কবি পাগলা কানাই কোন দিন কোন স্থানেই চাকরী গ্রহণ করেন নি। তবে, “কানাই বিশ্বাস, পিতা-তারিপ মণ্ডল, গ্রাম-বাড়িবাথান নামে একজন কামালউদ্দিন বিশ্বাসের ফকিরাবাদস্থ নীল কুঠির গোমস্তা ছিলেন”” । এখানেই সম্ভবত: ড. সাহেবের গোলমাল ঘটেছে। তা’ছাড়া, বেড়বাড়িতে কোনদিনই কোন নীল কুঠি ছিল বলে জানা যায় না।
প্রসংগত উল্লেখ্য যে, কামালউদ্দিন বিশ্বাস বাড়িবাথানস্থ শেরীফ সাহেবের নীল কুঠির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ফকিরাবাদে নীলকুঠি স্থাপন করেন । সে কুঠির আলামত এখনও পাওয়া যায় । শেরীফ সাহেবের অত্যাচারের প্রতিবাদ হিসাবে নিপীড়িত জনগণের সুবিধার্তে এটা স্থাপন করা হয়। এই নীলকুঠিতেই কানাই বিশ্বাস গোমস্তাগিরির কাজ করতেন।
নিঃসন্তান কামালউদ্দিন বিশ্বাস একজন জোতদার ও মহাজন ছিলেন । তিনি বছরে ৪০ প’তে অর্থাৎ ৬৪০ মন ধান প্রজাদের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে ধার-কর্জ দিতেন। এর জন্য তিনি কোন লাভ বা সুদ নিতেন না। “কোন কোন সময়ে বেড়বাড়ি এলাকায় এই ধান দাদন দেবার হিসাব- নিকাশের ভার পাগলা কানাই নিজে নিতেন এবং তিনিই এই ধান বন্টন করতেন । এর জন্য তিনি কিছুই নিতেন না” ।
বিশ্বাসী কবিকে বিশ্বাস করেই কামাল সাহেব এই ভার দিতেন। আমাদের বিশ্বাস, বর্ণনাকরীর বর্ণনায় ভ্রম বশতঃই ড. সাহেবের উক্ত ঘটনার বিকৃত রূপ দেখা দিয়েছে । প্রকৃতির পাগল কানাই-উজোল ছেলে বেলা থেকেই ছিলেন ভাবপ্রবণ। সারাদিন গুন গুন করে প্রকৃতির জয়গান করায় ছিল এদের বৈশিষ্ট্য। তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা রচনা করে সুর করে শোনানো কানাই-এর ছিল খেলা মাত্র।
তিনি কবিতা রচনা করেন, সুর দেন আর রাখাল বালকদের গেয়ে শোনান। দু’একজন পথিকও শোনে গান-সুর-কবিতা-ছড়া। ‘কানাই সুর করে গেতেন আর ছোট উজোল তালের ছাতির কুঁড়া, থালা-বাটি বা মাটির হাড়ি প্রভৃতি বাজিয়ে তাল দিতেন । বেড়বাড়িতে ফিরে এসে দু’ভাই সংগীত সাধনায় মগ্ন হলেন । অতি অল্প দিনের মধ্যেই কানাই গায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন এবং তা ছড়িয়ে পড়লো দেশ-বিদেশে।
ধুয়ো জারী গানের জগতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন। বলাবাহুল্য আমরা তাকে ধুয়ো-জারী গানের স্রষ্টা বলতে পারি। কারণ, তাঁর হাতেই এই গানের উৎকর্ষতা ও পূর্ণতা লাভ করে। শুধু শাস্ত্র সম্মত পদই তিনি রচনা করেন নি । রচনা করেছেন সে পদের সুর-ছন্দ-তাল-লয়-মাত্রা। মোট কথা, এক কালের পাগলা কবির সুরে আজ সবাই পাগল মাতোয়ারা। পাগলা কবি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের মন চষে ফিরতে লাগলেন। চারণ কবির মতো কথা বললেই তা হয়ে যায় ছন্দোবদ্ধ সুরে কবিতা।
কোন কবিতা বা গান রচনা করার জন্য তাকে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না। মুখ খুললেই মনের কথা বের হয় । এ প্রসঙ্গে কাঙ্গাল হরিনাথ বলেন, “তোরা তো সে গান শুনিশ নাই, কানাই-এর গান শুনিলে লোকে পাগল হইয়া যায়। আমরা অবাক হয়ে এই ১০ টি লোক ও বৃদ্ধ কানাই-এর সুরবাজী, সুরের খেলা শুনিতে লাগিলাম। ধন্য আওয়াজ, ধন্য শিক্ষা । আমি সে গানের বর্ণনা করিতে পারিলাম না, যাহারা সে গান শুনিয়াছেন, তাহারাই আমার কথা বুঝিতে পারিবেন” ।
এ উক্তি থেকেই আমরা বুঝতে পারি ‘চারণ কবি পাগলা কানাই’ কত বড় শক্তিশালী ও উঁচু মাপের কবি, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। শুধু তাই নয় শ্ৰীমান দূর্গাদাশ লাহিড়ী মহাশয় ‘কানাই সুর’ নামে এক নতুন ও অভিনব সুরের উল্লেখও করেছেন। এক কথায় আমরা বলতে পারি, সমসাময়িক কালেই শুধু নয়, সর্বকালে, সর্বশ্রেষ্ঠ লোক কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম ।
বিবাহ
চারণ কবি পাগলা কানাইয়ের বিবাহ সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করে বা কবির কাব্যে কোথাও কোন ইঙ্গিত পাই নি বটে, তবে কবি পৌত্র ইমদাদুল হক সাহেবের নিকট থেকে যে তথ্য আমরা জেনেছি তা সঠিক ও নির্ভুল বলে মনে করি । তিনি বলেন, ‘আমার দাদা পীর কেবলা নিরক্ষর কবি পাগলা কানাই ২৫ বছর বয়সে ১ লা বৈশাখ বিবাহ করেন। শ্বশুর পতুল্লাহ বিশ্বাস ছিলেন গ্রামের এক ভদ্র ঘরের সন্তান । তার দুই কন্যার প্রথমা কন্যা আমেনা খাতুন ১১ বছর বয়সে কবি পাগলা কানাইয়ের সাথে বিবাহ হয়।অপর কন্যাকে গ্রামেই বিবাহ দিয়েছিলেন। এই কন্যার শীতল ও মানিক নামে দুটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে ।
এতিম হবার পর বালকদ্বয় কবির নিকট পুত্রবৎ আশ্রয় পায়। কিন্তু তারাও কৈশোরেই ইন্তেকাল করে । আমেনা খাতুন গরীবের সন্তান হলেও তাঁর আচার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর ও সম্ভ্রান্ত স্তরের । রান্না-বান্নার কাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পটিয়সী । কবির মত স্ত্রীর দানের হাত ছিল অনেক লম্বা। ‘মিসকিন, ভুখা পাইলে তাহাকে না খাইতে দিয়া আপনারা খাইতেন না। এ সম্পর্কে কবি শিষ্য এলেম ফকির বলেন, “মার হাতের রান্না একবার খেলে সে স্বাদ আর ভুলা যায় না” ।
কথিত আছে, পাড়ার মেয়েরা গৃহ-কর্মে সাহায্য করে আমেনা খাতুনের কাছে রান্না ও কাঁথা সেলায় শিক্ষা করতো । শুধু তাই নয় প্রতিবেশী অতিথিবৃন্দের জন্য পিঠা তৈরি ও রান্নার কাজে ডাক পড়তো । তিনি ছিলেন অষ্টধাতুর গড়া সর্বগুণে গুণান্বিতা ।
দানে তিনি যেমন মুক্ত হস্ত ছিলেন, অতিথি সেবাও তাঁর জীবনের বড় বৈশিষ্ট ছিল। এলেম ফকির আরও বলেন, “ওস্তাদ মার হাতে না খেয়ে কোন দিনই ফিরতে পারি নি । কোন ফকির-মিসকিন খালি হাতে ফিরে গেছেন বলে শোনা যায় নি?
আমেনা খাতুন ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ মহিলা। কবির জীবনে এই ধর্মভীরুতা তার কাব্য জগতে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর স্বভাব, আচার-আচরণে ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গ্রামের দু’চারজন মেয়েদের সর্বদা কবিগৃহে দেখা যেত । কবি পত্নী সুমধুর সুরে কোরআন আবৃত্তি করতে পারতেন । কবি বিকেলে বসতো কোরআন শিক্ষার আসর। গ্রামের মেয়েরা দলে দলে এসে কোরআন শিক্ষা করতো। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন গ্রামের লোকেদের কাছে ব্যাংক স্বরূপ।
তাঁর কাছে তাদের টাকা-পয়সা, সোনা-রূপার গহনা প্রভৃতি দ্রব্যাদি আমানত থাকতো। কর্তব্যনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও পরোপকারী এই মহিয়সী মহিলা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কুড়িয়েছিলেন । আমেনা খাতুন অত্যন্ত রূপসী ছিলেন। সে রূপের গৌরব তাঁর ছিলনা। কবি স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। এ ভালবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর। কবির বহু গানে এর প্রমাণ পাওয়া যায় । এখানে একটা গানের কিয়দাংশ তুলে দিলাম-
বিবির সুরৎ যেন দুতিয়ের চাঁদ, আমি তালপাতার সিপাই ।
তার কলামে ভাইরে ভাই-
ওরে হাসলে বিবি দেখায় ছবি পটোর পটের পর।
আমার কাছে এলে পরে নড়ে যেন কল,
বিকলে যেন জলে ডোবা সুন্দীনালের ফল ।
সেই পিরিতি মজেরে ভাই, আছি ভবের পর ।

এক কথায় কবি পত্নীর রূপে-গুণে মুগ্ধ কানাই সম্পূর্ণরূপে তাহারই প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন।
১। কবির প্রতি পত্নির ভালবাসা ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ়। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন পুত্র ও ১ কন্যা। তারা হলেন-
২। জনাব গহর আলী শেখ। ইনি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। গহর আলীর একমাত্র পুত্র উসমান । উসমানের ২ কন্যা- রামেলা খাতুন ও জিয়ারন খাতুন।
৩। জনাব বাছের আলী শেখ । ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। বর্তমানে কবির বংশধর বলতে যারা আছেন তারা বাছের আলীর-ই সন্তান-সন্ত তি।
জনাব ইরাদ আলী শেখ। শৈশবেই (১৮৬২ খ্রি.) মারা যান ।
8। জনাবা রহিমা খাতুন । এই কন্যাকে কবি মির্জাপুর গ্রামে দামুল্য জর্দার- এর সাথে বিয়ে দেন। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরে তিনি মারা যান। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না।
আরও দেখুনঃ